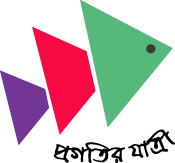বিজ্ঞান ভাবনা (৭৬): আশা নিরাশা – বিজন সাহা

কয়েক দিন আগে বাংলাদেশের মানুষ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও বিজয় দিবস পালন করল। এ উপলক্ষ্যে ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই লেখালেখি করেছে, করছে। আবার বিভিন্ন অনলাইন বা অফলাইন সভা সমিতিতে মানুষ তাদের পাওয়ার আনন্দ ও না পাওয়ার বেদনার কথা বলেছে, বলছে। অনেকেই মনে করেন যে লক্ষ্য, যে উদ্দেশ্য নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, যে জন্যে ত্রিশ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছিল আর দুই লক্ষ মা বোন নির্যাতিতা হয়েছিল পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দেশীয় দোসরদের হাতে, সে লক্ষ্য আজও অর্জিত হয়নি, বরং ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আমরা দিন দিন সেই লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আজকের বাংলাদেশে অনেক উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা আছে যারা অলিখিত নিয়ম থাকা সত্ত্বেও শহীদ মিনারে যায় না, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ বা জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে না, যা কিছু বাহান্ন, একাত্তর বা বাঙালি জাতিসত্তার সাথে জড়িত তা এড়িয়ে বা অবজ্ঞা করে চলে। একটা দেশের জন্ম একজন শিশুর জন্মের মতই। শিশু কোন প্রতিশ্রুতি নিয়ে জন্মায় না যদিও তাকে ঘিরে তার বাবা মা, আত্মীয়-স্বজনদের থাকে অনেক স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন কতটুকু সফল হবে বা আদৌ হবে কি না সেটা নির্ভর করে তার বাবা মা কিভাবে তাকে গড়ে তুলেছে তার উপর আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। এই একই কথা খাটে দেশের ক্ষেত্রেও। দেশের মানুষ দেশকে নিয়ে বিভিন্ন রকম স্বপ্ন দেখতেই পারে তবে দেশ ঠিক কেমন হবে সেটা নির্ভর করে দেশের নেতৃত্ব ও জনগন কিভাবে দেশ গড়ে তুলবে তার উপর। তাই আজ যখন অনেকেই স্বপ্ন ভঙ্গের কথা বলে তখন মনে প্রশ্ন জাগে এই স্বপ্ন কি সবাই দেখেছিল? যে লক্ষ্যের কথা আমরা বলি সেটা কি সবারই লক্ষ্য ছিল নাকি সেই লক্ষ্য ছিল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়া? নাকি এটা ছিল শুধু প্রগতিশীল ছাত্র জনতার স্বপ্ন যেটা বাস্তবায়নের কোন অবজেক্টিভ পরিবেশ দেশে কখনোই ছিল না। কারণ আমাদের ছাত্রও জীবনেও আমরা এক সময় ভাবতাম যাদের সাথেই কথা বলি তারাই সমাজতন্ত্রের কথা বলে, সমাজতন্ত্র গড়ার স্বপ্ন দেখে, তাহলে বাম দলগুলো ভোট পায় না কেন? এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে এক বন্ধুর স্ট্যাটাস যে লিখেছিল “আমি, আমার বন্ধু বান্ধব, আমার সন্তানরা, তাদের বন্ধু বান্ধব সবাই ট্রাম্পের বিপক্ষে, তাহলে ট্রাম্প জেতে কিভাবে?” এখানেও তাই আমাদের প্রথমে জানতে হবে আমরা যে বাংলাদেশের কথা বলি, যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি সেটা কয় জনের স্বপ্ন। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে না পাব ততক্ষণ আমাদের এই হতাশায় ভুগতে হবে। এমনও তো হতে পারে দেশের অধিকাংশ মানুষ আমাদের স্বপ্নের ভাগীদার নয়। তাহলে? সেক্ষেত্রে হতাশ না হয়ে তাদের আমাদের স্বপ্নের কথা বলতে হবে, তাদের বোঝাতে হবে বর্তমানের বাংলাদেশ নয় এক ভিন্ন বাংলাদেশ তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আরও ভাল ভাবে পূরণ করতে পারবে।
আর এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৯৪০ এর দশকে। মনে রাখতে হবে পাকিস্তান প্রস্তাবের মূল হোতারা ছিলেন এই বাংলা অঞ্চলের মানুষ আর এক পর্যায়ে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতাদের সক্রিয় আন্দোলন আর জনতার ভোটে পাকিস্তান পৃথিবীর আলো দেখে। যদিও সেই লাহোর প্রস্তাবে বাংলা ও বর্তমান পাকিস্তান অঞ্চলে দুটো আলাদা রাষ্ট্র (স্টেটস) গঠনের কথা ছিল, পরে কিভাবে যেন স্টেটস এর এস মুছে যায় আর দুটোর পরিবর্তে একটি মাত্র পাকিস্তানের জন্ম হয়। তবে দুটো হোক আর একটি হোক – পাকিস্তানের জন্ম হত ধর্মের ভিত্তিতে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু জন্মের অল্প দিনের মধ্যে শুরু হয় বিরোধ। প্রথমে ভাষার প্রশ্নে। পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও তাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিতে অস্বীকার করে সরকার। শুরু হয় আন্দোলন। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষার লড়াইয়ে প্রাণ দেয় এ দেশের ছাত্র জনতা। পরবর্তীতে ভাষার প্রশ্নে নমনীয় হলেও পূর্ব পাকিস্তানের উপর শোষণ চলতেই থাকে। ফলে তখন থেকেই শুরু হয় স্বায়ত্তশাসনের লড়াই যা ১৯৬৬ সালে চূড়ান্ত রূপ পায় ছয় দফার মাধ্যমে। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষে দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠায় ‘ছয় দফা দাবি’ পেশ করেন যা ‘বাঙালির বাঁচার দাবি’ হিসেবে পরিচিত। কী ছিল সেই ছয় দফায় —
দফা–১: শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি – লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদ সার্বভৌম হবে।
দফা–২: কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা – কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে— দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। বাকি সব বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।
দফা–৩: মুদ্রা বা অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা – মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দুটির যেকোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে (ক) সারাদেশের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে; অথবা (খ) বর্তমান নিয়মে সারাদেশের জন্যে কেবল একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে যেন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভেরও পত্তন করতে হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক বা অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।
দফা–৪: রাজস্ব, কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা – ফেডারেশনের অঙ্গরাজ্যগুলোর কর বা শুল্ক নির্ধারণের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো ধরনের কর নির্ধারণের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ-রাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর সব ধরনের করের শতকরা একই হারে আদায় করা অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।
দফা-৫: বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা (ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাজ্যের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে; (খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাজ্যগুলোর এখতিয়ারে থাকবে; (গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোনো হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোই মেটাবে; (ঘ) অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্য চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা করজাতীয় কোনো ধরনের বাধা-নিষেধ থাকবে না; (ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে বিদেশে নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি পাঠানো এবং নিজ স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।
দফা–৬: আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা – আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে নিজ কর্তৃত্বে আধাসামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।
এখানে আমরা দেখি এই ছয় দফা ছিল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থেকেই অধিকতর স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার দাবি। পরবর্তীতে এর সাথে আরও কিছু দাবি যোগ করে ১১ দফা প্রস্তাব সামনে আনা হয় যার স্থপতি ছিল মূলত ছাত্র সমাজ। ১৯৬৯ সালে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ প্রবল রূপ ধারণ করে। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচী পেশ করেন।
১. শিক্ষা সমস্যার আশু সমাধান। অর্থাৎ, হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত আইন বাতিল করা এবং ছাত্রদের সকল মাসিক ফি কমিয়ে আনা।
২. প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং পত্রিকাগুলোর স্বাধীনতা দেওয়া এবং দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনার নিষেধাজ্ঞা তুলে ফেলা।
৩. ছয় দফা দাবির প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা।
৪. পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশগুলোকে (অর্থাৎ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ,বেলুচিস্তান,পাঞ্জাব,সিন্ধু) স্বায়ত্তশাসন দিয়ে একটি ফেডারেল সরকার গঠন।
৫. ব্যাংক, বীমা, পাটকলসহ সকল বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ।
৬. কৃষকদের উপর থেকে কর ও খাজনা হ্রাস এবং পাটের সর্বনিম্নমূল্য ৪০ টাকা (স্বাধীনতার দলিলপত্রে উল্লেখ রয়েছে) ধার্য করা।
৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং শ্রমিক আন্দোলনে অধিকার দান।
৮. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৯. জরুরী আইন, নিরাপত্তা আইন এবং অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার।
১০. সিয়াটো (SEATO), সেন্ট্রো (CENTO)-সহ সকল পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং জোট বহির্ভূত নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ।
১১. আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি সহ দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি ও অন্যান্যদের উপর থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার।
এখানেও আমরা দেখি সেই পাকিস্তানের মধ্যে থেকেই একটা স্বায়ত্তশাসিত গণতান্ত্রিক দেশ গড়ার প্রতিজ্ঞা। তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র কখন এলো আমাদের আন্দোলনে? আমার ধারণা যদি ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে সরকার গঠনের সুযোগ দিতেন তাহলে অন্তত তখন মুক্তিযুদ্ধ হত না। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের কালো রাত আমাদের জন্য শাপে বর হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের উপর মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। একাত্তরে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছিল তাদের সিংহভাগ ছিলেন বামপন্থী। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁদের আদর্শ। আর সেই সাথে আসে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি প্রত্যাখান করার প্রশ্ন। আমার ধারণা এসব বুদ্ধিজীবীগণ তাঁদের কাজকর্ম দিয়ে সংবিধানে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সংযোজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আর তাঁদের হত্যা পরবর্তীতে দেশে এসব ধারণা জনমনে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে।
মনে রাখতে হবে যে বুদ্ধিজীবী মানেই প্রগতিশীল নয়। সেই সময় অনেক পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবীরা স্বাধীনতাকামী বুদ্ধিজীবীদের ধরিয়ে দেয়। আর পরবর্তীতে এরাই স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষানীতি ও রাজনীতিতে প্রবেশ করে এখানে পাকিস্তানপন্থী রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটায়। বর্তমানে অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই কোন না কোন দলের সমর্থক, ফলে তারা যতটা না দেশের স্বার্থে তারচেয়ে বেশি দলের স্বার্থে কাজ করে। অথচ বুদ্ধিজীবীদের হওয়া উচিৎ জাতির বিবেক। একাত্তরের বুদ্ধিজীবী হত্যার মাসুল আমরা এখনও দিয়ে যাচ্ছি। ১৯৭১ সালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন পরবর্তীতে সংবিধানে সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের পাশাপাশি সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ দুটকে স্থান করে দিয়েছে। যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে শেখ মুজিবকে ঘিরে মানুষের আবেগ এতটাই তুঙ্গে ছিল যে তিনি বলতে গেলে একক ভাবে এই শব্দগুলো সংবিধান ভুক্ত করেছেন। কারণ আওয়ামী লীগের তখনকার যে শ্রেণি চরিত্র তাতে স্বাভাবিক ভাবে এসব শব্দ সংবিধানে আসার কথা ছিল না। আর সেটা ছিল না বলেই ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের সাথে সাথে আওয়ামী মন্ত্রী সভার প্রায় পুরোটাই মুস্তাকের অধীনে শপথ নেয়। বর্তমান আওয়ামী লীগও ভিন্ন কিছু নয়। তাই তারাও যে বাহাত্তরের সংবিধানের জন্য লড়াই করবে না সেটাই স্বাভাবিক।
মনে পড়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সেই ছড়ার কথা?
সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে
কিন্তু কথাটা হচ্ছে শুধু মনে মনে বললেই হবে না, কাজ করতে হবে। প্রতিজ্ঞার সাথে সাথে সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য দরকার নিরলস শ্রম। মার্ক্সের ভাষায় – এতদিন দার্শনিকরা পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করেছেন, এখন সময় এসেছে তাকে পরিবর্তন করার। কিন্তু কিভাবে? এটা ঠিক, বাহাত্তরের সংবিধান আমাদের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক দলিল। কিন্তু সেটা কি মানুষ জানে, সেটা কি মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়েছে? তারা কি জানে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, বরং সবার ধর্ম পালন করার বা না করার সাংবিধানিক অধিকার, কারও উপর কারও ধর্মীয় অনুশাসন চাপিয়ে দেওয়া নয়, সবাইকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করার অধিকার দেয়া। আজ পশ্চিমা বিশ্বের সাথে অন্যদের যুদ্ধ এ নিয়েই। কিভাবে? বিগত অনেক বছর হল ইউরোপের অনেক দেশে ক্রিস্টমাস ক্রিস্টমাস নামে পালন না করার চেষ্টা করা হয়। কেন? তাতে অন্য ধর্মের মানুষদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে। এটা ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, এটা এক দলের মন রক্ষায় অন্য দলের উপর কিছু মত জোর করে চাপিয়ে দেয়া। ধর্মনিরপেক্ষতা হল সেই পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে সবাই নিজ নিজ ধর্ম এমন ভাবে পালন করে যাতে অন্য ধর্মের মানুষ সেটাকে নিজের উৎসব বলে মনে করতে পারে। মানে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।
প্রশ্ন আসতে পারে দেশে কি কখনও ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল? না থাকলে আমরা কিভাবে সেটা প্রতিষ্ঠা করব। আমার ধারণা ছিল। আসলে একটা জাতির মূল পরিচয় শুধু তার ধর্ম নয়, তার লোকজ সংস্কৃতি, তার ভাষা। ফলে বিভিন্ন দেশে বাস করেও কুর্দিরা নিজেদের একই জাতি মনে করে, আবার একই ভাষাভাষী ও একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের আরবেরা নিজেদের ভিন্ন মনে করে। এ এক জটিল প্রক্রিয়া। ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি সবই জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তবে সংস্কৃতির বন্ধন অনেক মৌল। ফলে একদিকে যেমন ধর্মীয় বন্ধন ভারত থেকে পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছিল, একই ভাবে ভাষা ও সংস্কৃতির বন্ধন জন্ম দিয়েছে বাংলাদেশ। আর এই বন্ধন গড়ে উঠেছে দৈনন্দিন জীবন যাত্রা, জারি গান, কবি গান, বাউলের গান, কীর্তন, যাত্রা পালা, বিভিন্ন মেলা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। তাই যা কিছু মানুষকে একে অন্যের কাছে নিয়ে আসে, যা কিছু মানুষে মানুষে ঐক্য সৃষ্টি করে তাকে সামনে আনতে হবে। আর যা কিছু বিভেদের জন্ম দেয় তাকে দূরে সরাতে হবে। তাহলে কি আমরা ধর্মকে দূরে সরিয়ে দেব? না। ধর্ম আগেও ছিল আর এই ধর্মের মধ্যে থেকেই মানুষ একে অন্যের সাথে মেলামেশা করেছে, পূজায় গেছে, ঈদ করেছে, বিভিন্ন মেলায় অংশ নিয়েছে। কিন্তু ধর্মের নামে যখন বিভিন্ন ওয়াজে বিভেদের বাণী শোনানো হয় সেটাকে বন্ধ করতে হবে। রাষ্ট্র সব নাগরিককের অধিকার রক্ষা করতে বাধ্য। তাই যখন কেউ ওয়াজে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ায় সেটা রুখতে হবে। রাষ্ট্র যদি রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের বিভেদ ছড়ানোর নামে আটকে রাখতে পারে, সে কেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক কথাবার্তার জন্য কাউকে আটকাতে পারবে না? যদি আমরা পাকিস্তান আমলের দিকে খেয়াল করি, দেখব লাহোর প্রস্তাব হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতেই আর পাকিস্তানে যে আন্দোলন সেটা হয়েছে ভাষা আর সংস্কৃতিকে ঘিরে। যখন রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ছিল তখন সাংস্কৃতিক কর্মীরাই আন্দোলনকে সামনে নিয়ে গেছে। ছায়ানট ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠন এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই আজ সেখান থেকেই শুরু করতে হবে।
বাহান্নয় আমরা ভাষার জন্য লড়েছিলাম। আজ ইউক্রেনে যে যুদ্ধ সেটার শুরু এই ভাষা আর সংস্কৃতি নিয়েই। একুশ আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এটা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বাঙালির অবদান। ধর্মনিরপেক্ষতা হতে পারে আরেকটা মাইল স্টোন। আগেই বলেছি ইউরোপে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে এই অজুহাতে ক্রিস্টমাস আজ অন্য নামে পালিত হচ্ছে। এটা আসলে সমস্যার সামাধান নয়, সমস্যা তৈরি করা। একদলকে, তা সে সংখ্যাগুরুই হোক আর সংখ্যালঘুই হোক, খুশি করতে গিয়ে অন্য দলের অধিকার হরণ এটাই দ্বিজাতিতত্ত্ব। আর ধর্ম বা দল নিরপেক্ষতা হল সবাইকে তার অধিকার ভোগ করতে দেয়া। এবং এমন পরিবেশ তৈরি করা যাতে সবাই নিজ নিজ ধর্মীয় বা অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করতে পারে অথচ অন্যদের অধিকার লঙ্ঘন না করে। ধর্মনিরপেক্ষতা – এটা কাউকে অধিকার বঞ্চিত করা নয়, সবাইকে অধিকার ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া।
আমাদের বুঝতে হবে যে ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল আমাদের কাছে অনেকটা লটারি জেতার মত। কিন্তু তখনকার গ্রাউন্ড রিয়ালিটি আমাদের সেটা ধরে রাখতে দেয়নি। তাই হারানোর বেদনা আমাদের যেন কষ্ট না দেয়। আর সেটা যাতে আমরা ফিরে পাই সেটাই যেন আমাদের আমাদের লক্ষ্য হয়। স্বাধীনতার পরে বা এখনও পর্যন্ত অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে রাজনীতি করলেও জনগণকে সেটা খুলে বলেনি। এর বিরোধীরা যত অপপ্রচার করেছে, করছে তার বিপরীতে আমরা শুধু স্লোগান দিয়েছি। মানুষকে বোঝাতে হবে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, ধর্মনিরপেক্ষতা হল সবার নিজ নিজ ধর্ম পালনের সাংবিধানিক অধিকার। এ থেকে কাউকে বঞ্চিত করা মানে সংবিধান পক্ষপাতদুষ্ট। আর আইন যখন পক্ষপাতদুষ্ট হয় সে তখন অসাম্য তৈরি করে, তাতে তখন অন্যায় করার সুযোগ ও প্রবণতা দুটোই বেশি থাকে। তাই দেশের ও দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বার্থেই আমাদের দরকার ধর্মনিরপেক্ষতা। একজন মানুষকে অসুখী করে সংসারে যেমন শান্তি আনা যায় না, দেশের ক্ষেত্রেও তাই। সুতরাং আসুন আমরা হতাশায় না ভুগে আশার বাণী ছড়াই।
আগেই বলেছি বর্তমানে একাত্তরের লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে বড় বাধা আমরা এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের ভূত ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সেটা তাড়ানো জরুরি। কীভাবে? একুশ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাবার পরে কী ভাষা আন্দোলন, কী বাংলা তথা মাতৃভাষা ইতিহাসে নিজেদের স্থান চিরস্থায়ী করে নিয়েছে। এরকম কিছু একটা আমাদের দরকার। আর সেটা আমাদের নাগালের মধ্যে। একাত্তরে ত্রিশ লাখ মানুষের হত্যা আজও জেনোসাইড বলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। আমাদের ইতিহাসে এটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এখন আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে হবে জেনোসাইডের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করতে। শুধু তাই নয় দেশেও জেনোসাইড শব্দটা আমাদের সামনে নিয়ে আসতে হবে। আজ নতুন প্রজন্মের অনেকেই একাত্তরের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানে না, আর সে কারণেই শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সমর্থন করে। আমার ধারণা ২১ ফেব্রুয়ারি যেমন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পেয়েছে একাত্তরের হত্যাকাণ্ড যদি তেমনি জেনোসাইড হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় তাহলে দেশে পাকিস্তানী প্রভাব অনেকাংশেই কমবে। সেটাই দেশকে একাত্তরের চেতনা বিকাশে পথ দেখাবে।
নতুন বছর দরজায় টোকা দিচ্ছে। প্রগতির যাত্রীর পাঠকদের জানাই কৃতজ্ঞতা – সাথে থাকার জন্য, ধৈর্য ধরে পড়ার জন্য। জানি অনেকেই আমার সাথে একমত প্রকাশ করেন না, সেটা দরকারও নেই। তবে সব কিছুই যে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, অন্য ভাবে ভাবা যায় – সেটা বলাই এসব লেখার মূল উদ্দেশ্য। কারণ একমাত্র তখনই মানুষ প্রশ্ন করে, জানতে চায়। প্রশ্ন করা, জানতে চাওয়া – সেটাই বিজ্ঞানমনস্কতা। সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা।
গবেষক, জয়েন্ট ইনস্টিটিউট ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ
শিক্ষক, রাশিয়ান পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি, মস্কো