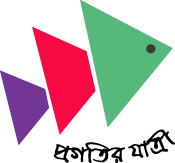বিজ্ঞান ভাবনা (১৩৪):বিজ্ঞান ও রেটিং-বিজন সাহা

গত দুই পর্বে আমরা বিজ্ঞান বা সঠিক ভাবে বললে বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা নিয়ে বলেছি। এই পর্বে সেটাই ভিন্ন দিক থেকে দেখব। প্রথমেই আসি রেটিং সিস্টেমে। গবেষণার কাজে মূল যেটা দেখা হয় সেটা হল পাবলিকেশন। কারণ এখানে অন্য কোন মাপকাঠি নেই কারো সক্রিয়তা বিচার করার জন্য। যদি ছাত্রদের পরীক্ষা থাকে, শিক্ষকদের ক্ষেত্রে থাকে তাঁদের পড়ানোর দক্ষতা, কারণ ছাত্রদের সাফল্য শিক্ষকদের ভালো পড়ানোর উপর অনেকটাই নির্ভরশীল, তবে গবেষকদের সেরকম কোন মানদণ্ড নেই। তাঁদের কাজের স্বীকৃতি আসে গবেষণার ফলের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সেটা আমরা কিভাবে জানব? আগেই বলেছি গবেষণা পত্র প্রকাশ গবেষণার শেষ ধাপ, যদিও পরবর্তীতে অন্যদের কাজকর্মে সেই পেপারের উল্লেখ বা রেফারেন্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সেটার মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি যে প্রাপ্ত ফলাফল কমিউনিটির কাজে লাগছে। এটা অনেকটা ফটোগ্রাফারদের ছবি তোলার মত। এখন অবশ্য যুগ পাল্টিয়েছে, তবে ডিজিটাল ক্যামেরা আসার আগে পর্যন্ত প্রিন্ট ছিল ফটোগ্রাফারের কাজ মূল্যায়ন করার একমাত্র উপায়। আগে যখন রেটিং সিস্টেম ছিল না, তখন যেকোনো স্বীকৃত জার্নালে পেপার পাবলিশ করলেই হত, যদিও তখনও ভালো জার্নালের দাম ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল জার্নাল ভালো কি মন্দ সেটা ঠিক হবে কিভাবে। তার অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে। প্রথমত রিভিউ তো আছেই, আরও আছে সেই জার্নালের পেপারগুলো অন্যরা কতটুকু রেফার করছে। তার মানে এখন একজন গবেষক আগের মত শুধু গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন না, তার আগে দেখেন সেই জার্নালের রেটিং। শুধু তাই নয় কোন জার্নালে পেপার বেরুচ্ছে, সেই পেপার কতজন রেফার করছে ইত্যাদির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে গবেষকের রেটিং। আজকাল প্রায়ই দেখবেন অমুক বিশ্বের ২% বা ৩% বা ৫% বিজ্ঞানীর মধ্যে স্থান পেয়েছেন। এর অর্থ হল তার ভালো জার্নালে পাবলিকেশন আছে, সেটা অন্যেরা রেফার করছে। আবার এই রেফারেন্স নিয়েও অনেক কথা আছে। আমি নিয়মিত ই-মেইল পাই বিভিন্ন গবেষকের কাছ থেকে তাঁদের নতুন পাবলিকেশন সহ। এর মানে তাঁরা চান আমার কাজে যেন আমি এদের পেপার রেফার করি। অনেকটা মনে হয় গবেষকরা যেন মুদি দোকান খুলে বসে আছেন নিজের পেপার বিক্রি করার জন্য। হতে পারে আমি এখনও ততটা স্মার্ট নই। ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিজে এ ব্যাপারে কাউকে অনুরোধ করি না, কেমন যেন নিজেকে খেলো মনে হয়। আর কোন কাজ আমার কাজের সাথে সম্পর্কিত হলে তাঁদের বলার আগেই সেটা রেফার করি। মনে পড়ে বছর পনের আগের কথা। তখন প্রচুর ফটো সাইট ছিল। আমি নিয়মিত সেখানে ছবি আপলোড করতাম। কখনও কখনও দিনের সেরা ছবি হত আমার কাজ। অনেক সময় কেউ কেউ লিখত আমি তোমার ছবিতে লাইক দিলাম, তুমি আমার ছবিতে দিচ্ছ না কেন। এ যেন ছবি আমার পছন্দ হল কি হল না সেটা বড় কথা নয়, আমি দিয়েছি আমাকে দাও। এভাবেও অনেক সিটেশন হয়। মানে এখানেও খেলার মাঠ আর ততখানি স্পোরটিং নয়, এখানেও ফিক্সিং। আচ্ছা সত্তরের দশকে কি ক্রিকেটে ম্যাচ ফিক্সিং ছিল? মনে পড়ে না। এসব শুরু হল যখন খেলায় টাকার বন্যা বয়ে গেল। একই ভাবে যখন থেকে গবেষকদের প্রোমোশন, সম্মান এসব রেটিং নির্ভর হল, তারাও তখন কাজের পাশাপাশি অন্যেরা যাতে সেই কাজের প্রশংসা করে সে ব্যাপারে চিন্তিত হন। এটাও অনেকটা ফেসবুকে লাইকের মত। আজকাল অনেকেই নিজেদের লেখা নিজেরাই লাইক দেয়। কয়েকদিন আগেও সেটা কেমন যে বিশ্রী মনে হত। তবে সেদিন শুনলাম যদি স্ট্যাটাসে লাইক না পড়ে সেটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়, তাই নিজের পোস্টে নিজে লাইক দিলে সেটা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অর্থাৎ আজ জীবনের এলগরিদম আমাদের এসব করতে বাধ্য করছে।
যখন পিএইচডির ছাত্র ছিলাম দুই কলম ক্যালকুলেশন করেই মনে হত একটা পেপার লেখা দরকার। সুপারভাইজারকে এ ব্যাপারে বললে বলতেন এত ব্যস্ত না হতে। দুবনায় কাজের প্রথম বছরগুলোতেও এরকম হত। এখন একটা কাজ শেষ করার পর বেশ কিছুদিন ফেলে রাখি। কারণ সেসময় কাজের দ্বারা এতটাই আবিষ্ট থাকি যে ছোটখাটো ভুল চোখে পড়ে না। তখন যদি পাবলিকেশনের সংখ্যাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হত এখন প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করা মূল মনে হয়। তাই যখন দেখি কেউ কেউ একের পর এক পেপার পাবলিস করে যাচ্ছে অবাক হই। কেননা এমনিতেই নিজের পাওয়া রেজাল্ট হজম করতেও বেশ কিছুদিন সময় লাগে। কিন্তু ঐ যে বললাম না, চাই বা না চাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতেই হয়। যারা মধ্য মানের গবেষক স্রোত তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় বা তাঁরা ভেসে যেতে বাধ্য হয়। খুব কম লোকই পারে এই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকতে। এ নিয়ে নোবেলজয়ী প্রফেসর হিগসের এক সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম। ইনি সেই হিগস যার হিগস বোসন ঈশ্বর কণা নামে পরিচিত। তিনি লিখেছেন বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষক ও গবেষকদের কাছ থেকে এত বেশি পাবলিকেশন চায় যে তাঁর চাকরি থাকবে কিনা সে ব্যাপারে তিনি সন্দিহান হয়ে ওঠেন। কারণ তিনি প্রতি বছর একের পর এক পেপার লিখতে মানসিক ভাবে প্রস্তুত নন। ভালো কাজের জন্য সময় দরকার। বিগত অনেক বছর প্রায় কোন রকম পাবলিকেশন না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর চাকরির নবায়ন নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন। শুধুমাত্র তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলেই তিনি বেঁচে গেছেন। সমস্যা হল সবাই হিগস নন। আসলে আগে যদি তুলনামূলক কম লোকজন গবেষণার সাথে জড়িত থাকতেন তবে আজ অসংখ্য মানুষ গবেষণা করেন। কোন কোন পেপারে কয়েক পৃষ্ঠা শুধু লেখকদের নাম লিখতেই চলে যায়। বিশেষ করে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের উপর যেসব এক্সপেরিমেন্ট হয় সেখানে শত শত লোক অংশ নেয়। তাছাড়া বিজ্ঞান আজকাল এতটাই জটিল হয়ে গেছে যে হাজার হাজার গবেষক স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ কাজ করে যান। কেউ স্বীকৃতি পায়, কেউ পায় না। তবে অধিকাংশ যুগান্তকারী কাজ অন্যান্য অসংখ্য কাজের উপর ভিত্তি করেই হয়। আমার শিক্ষক বলতেন পদার্থবিদ্যায় ঋণাত্মক ফলও ফল, কেননা সেটা থেকে অন্যেরা জানবে কোন পথে যেতে নেই। আর তাই নিজের যদি সামান্য অবদান থাকে গবেষকের উচিৎ সেটাও প্রকাশ করা। কারণ তা পরবর্তী কাউকে সঠিক পথে যেতে সাহায্য করবে, সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করবে। আর এজন্য হলেও এমন সব জার্নালে নিজের গবেষণা প্রকাশ করার চেষ্টা করা দরকার যাতে সেটা বেশি সংখ্যক বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিগোচর হয়।
এসব দিক থেকে বর্তমানের রেটিং সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তার নেগেটিভ দিকও আছে। এটা অনেকটা কুইজ সিস্টেমের মত। নম্বরের কথা মাথায় রেখে ছাত্ররা প্রশ্নের উত্তর মুখস্ত করতেই বেশি আগ্রহী আসল জ্ঞান অর্জন করার চেয়ে। একই ভাবে এই সিস্টেম অনেককে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে কোন গবেষণা করার চেয়ে বেশি বেশি পেপার লিখতেও আগ্রহী করে তুলতে পারে। কারণ গবেষণার ফল তখন যতটা না কাজের কনটেন্ট তারচেয়ে বেশি পাবলিকেশনের সংখ্যা, ফলে পেপার পাবলিশ করাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। একজন ছাত্র জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়াশুনা করবে নাকি নম্বর পাওয়ার জন্য সেটা যেমন তার উপর নির্ভর করে একই ভাবে একজন গবেষক প্রকৃতির রহস্য জানার জন্য গবেষণা করবেন নাকি আরও একটা পাবলিকেশনের জন্য সেটাও তাঁর উপর নির্ভর করে। তবে যেহেতু মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন করা ও প্রকৃতির রহস্য জানা তাই নম্বর বা পাবলিকেশন গুরুত্বপূর্ণ হলেও লক্ষ্যটা ভিন্ন হওয়া সঙ্গত। এর উপর নির্ভর করে ছাত্র বা গবেষকের সততা। তবে বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা মূলত রেজান্ট ওরিয়েন্টেড বা ফলকেন্দ্রিক, কাজের আনন্দ নয়, ফলের জন্যই কাজ। তাই ইচ্ছা অনিচ্ছায় এই ইঁদুর দৌড়ে অধিকাংশ গবেষককেও অংশ নিতেই হয়।
গবেষক, জয়েন্ট ইনস্টিটিউট ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ
শিক্ষক, রাশিয়ান পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি, মস্কো