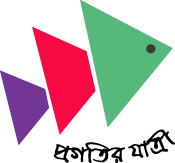বাংলার বারভূঁইয়া বা বারো ভূঁইয়াদের বিদ্রোহ ও পতন যেভাবে হয়েছিল

বাংলায় তখন আফগান সুলতানরা বহু বছর ধরে অনেকটা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে আসছিলেন। বহু বছর ধরে এই অঞ্চলে থাকার কারণে এই শাসকরা অনেকটা এদেশের বাসিন্দা হয়ে উঠছিলেন।
সেই সময় দিল্লির মসনদে একটা বড় পরিবর্তন এসেছে। বেশ কিছু বছর আগে অর্থাৎ ১৫২৬ সালে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে আফগান শাসক ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লির ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে মুঘলরা।
বাবরের ছেলে হুমায়ুনের মৃত্যুর পর অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় ক্ষমতায় আসেন মুঘল সম্রাট আকবর। কিন্তু তার সময়কালকেই বলা হয় মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সোনালি সময়।
পুরোপুরি রাজ্যভার গ্রহণ করার পর আকবর নজর দেন বাংলার দিকে। এজন্য অবশ্য বড় কৃতিত্ব দেয়া হয় আকবরের অর্থমন্ত্রী টোডরমলকে।
বলা হয়, তিনিই প্রধান আবিষ্কার করেন যে, বাংলা অঞ্চল ফসলি আর উর্বর হওয়ায় এই এলাকা থেকে বিপুল রাজস্ব আহরণ করা সম্ভব।
বাদশাহ আকবর তাকে ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার নবাব করে পাঠান। দায়িত্ব নেয়ার পরেই তিনি চেষ্টা শুরু করেন, কীভাবে বঙ্গদেশ থেকে আয় বৃদ্ধি করা যায়। সেজন্য সবার আগে পুরো বঙ্গ অঞ্চলে মুঘলদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দরকার ছিল।
কিন্তু তাদের সেই চেষ্টায় সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাংলার বারো ভূঁইয়ারা।

বারভূঁইয়া বা বারো ভূঁইয়া কারা?
‘বাংলার ইতিহাস’ গ্রন্থে সুনীতি ভূষণ কানুনগো লিখেছেন, “১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল বাহিনীর হাতে দাউদ খান কররানীর পরাজয়ের ফলে বাঙ্গালায় দীর্ঘ আড়াইশত বছরের স্বাধীন সুলতানতের পতন ঘটে।
রাজধানীতে কররানী শাসনের পতন ঘটিলেও বাঙ্গালা রাজ্যের আঞ্চলিক শাসনকর্তারা এবং প্রতিপত্তিশালী ভূস্বামীরা কেবল স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহারা এককভাবেই হোক আর সম্মিলিতভাবেই হোক মুঘল সম্প্রসারণ প্রতিরোধ করিতে তৎপর হইয়া উঠেন,” তিনি লিখেছেন।
“এই প্রতিরোধকারী নেতারা সমসাময়িককালের দেশি বিদেশি ইতিহাস গ্রন্থে বারভূঁইয়া নামে পরিচিত।”
সুলতান দাউদ খান কররানী পরাজিত হওয়ার পর বাংলা অঞ্চল একক কোন শাসকের অধীনে ছিল না।
সেই সময় ছোট ছোট অংশে ভাগ করে বাংলার বিভিন্ন এলাকা শাসন করতেন একেকজন ছোট ছোট নৃপতি বা রাজা বা জমিদাররা।
তখনকার আঞ্চলিক শাসনকর্তা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করে কাজ করতে শুরু করলেন। অনেকে মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে তোলেন।
ইতিহাসবিদদের মতে, সেই সময় বাংলা এলাকা জুড়ে এরকম শাসক ছিলেন শতাধিক। কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল প্রভাবশালী। বিশেষ করে মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোয় তারা বিশেষ নজর কেরেছিলেন।
পরবর্তীতে আকবর নামা এবং মির্জা নাথানের বাহরিস্তান-ই-গায়েবীতে এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরাই পরিচিতি পেয়েছিলেন বারো ভুঁইয়া নামে।
তখনকার আঞ্চলিক শাসনকর্তা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করে কাজ করতে শুরু করলেন। অনেকে মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে তোলেন।
বারভূঁইয়া বা বারো ভূঁইয়া নাকি বড় ভূঁইয়া?
ভূঁইয়া শব্দের অর্থ হলো ভৌমিক বা ভূস্বামী- যিনি প্রচুর জমির অধিকারী। মধ্যযুগে এই শাসকরা তাদের এলাকার সব জমির মালিক ছিলেন, প্রজারা তাদের খাজনা দিয়ে এসব জমিতে চাষবাস করতেন। পরবর্তীকালের জমিদারী ব্যবস্থার মতো।
এরকম শতাধিক ভূঁইয়া থাকার পরেও কেন বারো ভূঁইয়াকে নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়, এ নিয়ে ইতিহাসবিদরা কখনো একমত হতে পারেননি।
অনেকের মতে, আকবরনামা বা বাহারিস্তান-ই-গায়েবীর মতো গ্রন্থগুলোয় বারো জন ভূঁইয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
এদের কেউ কেউ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, কেউ কেউ মুঘলদের অনুগ্রহ ভাজন ছিলেন।
আবার কোন কোন ইতিহাসবিদের মতে, শব্দটা আসলে বড় ভূঁইয়া বা বড় শক্তির ভূঁইয়া থেকে বারো ভূঁইয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে।
ইতিহাসের সেই সময়ের বিভিন্ন বর্ণনায় বারো ভূঁইয়াদের সম্পর্কে নানারকম বর্ণনা পাওয়া যায়। এদের সংখ্যা নিয়েও বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য এসেছে।
তবে মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।
এটা পরিষ্কার যে, বাংলায় অনেক ভূঁইয়া ছিলেন। তাদের বড় একটি অংশ মুঘলদের শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।
তবে প্রভাব আর বীরত্বের জন্য বেশ কয়েকজনের নাম আলাদাভাবে ইতিহাস গ্রন্থে উঠে এসেছে।

বাংলার বিভিন্ন এলাকা শাসন করতেন একেকজন ভূঁইয়া
সুনীতিভুষণ কানুনগো লিখেছেন, সেই সময় ময়মনসিংহের পূর্বাংশ, কিশোরগঞ্জ ও সিলেটের একটি অংশ এবং ঢাকার উত্তর দিকে একটি অংশ নিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা ভাটি এলাকা নামে পরিচিত ছিল।
সেই ভাটি অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন ঈসা খাঁ, যাকে মসনদ-ই আলা উপাধিতে অভিহিত করেছেন কোন কোন ইতিহাসবিদ।
“প্রতাপ প্রতিপত্তির দিক থেকে তিনি বারভূঁইয়াদের মধ্যে কেবল সর্বশ্রেষ্ঠই ছিলেন না, তিনি তাহাদের দ্বারা অবিসম্বাদী নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন।”
‘বারভূঁইয়া বা ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস’ বইতে আনন্দনাথ রায় লিখেছেন, ঈশা খাঁর পরিবার অযোধ্যা থেকে বাণিজ্য করার জন্য বঙ্গদেশে এসে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন।
পরে সোনারগাঁয়ের কাছে জমি কিনে বসবাস করতে শুরু করেন। আফগানদের রাজকর না দিয়ে বিদ্রোহ করায় তার পিতাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল।
সেই সময় ঈশা খাঁর পিতৃব্য কুতুব খাঁ রাজ আনুকূল্য অর্জন করেছিলেন। বাহ্যিক আচরণের মাধ্যমে তিনি বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করলেও বরাবর স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করেছিলেন।
তিনি বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন বলে ইতিহাসবিদরা লিখেছেন।
মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঈশা খাঁ বহুবার সন্ধি করেছেন, আবার বিদ্রোহীও হয়েছেন।
আনন্দনাথ রায় লিখছেন, “প্রবাদ রয়েছে, ঈশা খাঁকে দমন করার জন্য মুঘল সেনাপতি মানসিংহ সোনারগাঁয়ের খিজিরপুর দুর্গ অবরোধ করেন। সেই যুদ্ধে মানসিংহের জামাতা নিহত হলে তিনি ঈশা খাঁকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহবান করেন।
উভয়ের মধ্যে লড়াইয়ের একপর্যায়ে মানসিংহের তলোয়ার ভেঙ্গে যায়। তখন মানসিংহকে হত্যা না করে বরং স্বহস্তের তলোয়ার সমর্পণ করেন ঈশা খাঁ। তখন ঈশা খাঁ চিরদিন মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করবেন বলে ঘোষণা করেন।”
তখন তাকে সোনারগাঁয়ের সর্বময় শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেন মানসিংহ। ঈশা খাঁ জীবিত থাকা পর্যন্ত আর মুঘল বাদশাহের বিরুদ্ধাচরণ করেননি।
তবে এটি লোকগাঁথা হিসেবেই প্রচলিত, এই ঘটনার ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ নেই বলে বলেন ইতিহাসবিদেরা।
যদিও ঈশা খাঁর উত্তরাধিকারী মুসা খাঁ মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। পরবর্তীকালে বারোভূঁইয়াদের বিদ্রোহের মূল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুসা খাঁ।

বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে সুনীতি ভূষণ কানুনগো লিখেছেন,ঘোড়াঘাট অঞ্চলে শাসক ছিলেন মাসুম খান কাবুলি। চাটমোহরে তার এবং ছেলে মির্জা মুমিনের শাসন কেন্দ্র ছিল।
মুঘলদের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন মাসুম খান কাবুলি। কিন্তু মানসিংহের আক্রমণের মুখে প্রথমেই ঘোড়াঘাটের পতন ঘটে। মাসুম কাবুলি পালিয়ে ঈশা খাঁর এলাকায় আশ্রয় নেন।
তার সম্পর্কে আনন্দনাথ রায় লিখেছেন, তখন বাঙ্গালায় মাসুম কাবুলি এবং সোনারগাঁয়ে ঈশা খাঁ পাঠান দলের প্রকৃত নেতা ছিলেন।
শাহজাদপুরের ভূস্বামী ছিলেন রাজা রায়। তিনি সুবাদার ইসলাম খানের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নেন।
ঢাকার উত্তরাঞ্চলের উঁচুভূমি নিয়ে ভাওয়াল অঞ্চল পরিচিত ছিল। সেখানকার জমিদার ছিলেন ফজল গাজী।
তার মৃত্যুর পর শাসক ছিলেন বাহাদুর গাজী এবং তার ভাইয়ের ছেলে আনোয়ার গাজী। তারাও মানসিংহের কাছে পরাস্ত হয়ে মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল।
ঢাকার বিক্রমপুরের জমিদার ছিলেন কেদার রায়। তবে মানসিংহের অভিযানে পরাজিত হলে তখনকার শ্রীপুর বা বর্তমানের বিক্রমপুর মুঘলদের হাতে আসে।
নিয়মিত কর দেয়ার শর্তে তাকে রাজ ক্ষমতায় থাকতে দেন মানসিংহ। তিনি কেদার রায়ের একজন কন্যাকে বিয়েও করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে আবার বিদ্রোহী হয়েছিলেন কেদার রায়। পরে মুঘলদের সাথে যুদ্ধে তার মৃত্যু হয়।
আনন্দনাথ রায় লিখেছেন, “বার-ভূঁইয়াদের মধ্যে যদি কাহাকেও সর্বপ্রথম আসন প্রদান করতে হয়, তাহা রাজা কেদার রায়ের প্রাপ্য। কারণ ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলী ছিলেন বা সর্বপ্রধান ছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও মুঘল পতাকামূলে মস্তক অবনত করতে বাধ্য হন।
পরবর্তীতে অধিকাংশই সেই পথ বেছে নেন। কিন্তু অবনত হননি কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য ও মুকুন্দ রায়।”
মুসা খার নেতৃত্বে বারো ভূঁইয়াদের সম্মিলিত বাহিনী মুঘলদের মুখোমুখি হয় বিক্রমপুরে ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে। সেই যুদ্ধেই বন্দি হওয়ার পর কেদার রায়ের মৃত্যু হয়।
সেই সময় ময়মনসিংহ, শেরপুর এলাকা নিয়ে চাঁদ পরতাব জমিদারী ছিল, যার ভূঁইয়া ছিলেন বিনোদ রায়।
বর্তমান ফরিদপুর সে সময় পরিচিত ছিল ফতেয়াবাদ নামে। এর শাসনকর্তা ছিলেন বারভূঁইয়াদের অন্যতম নেতা মজলিশ কুতুব। তার নিজস্ব একটি নৌবাহিনী ছিল।

যশোর এলাকার ভূঁইয়া ছিলেন শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য। তার ছেলে প্রতাপাদিত্য এবং পৌত্র উদয়াদিত্য- উভয়েই মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভূমিকা রেখেছিলেন।
শ্রীহট্ট বা বর্তমানের সিলেট এলাকার জমিদার ছিলেন বায়েজিদ করবারী। তিনি দীর্ঘদিন মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন।
হিজলী, মেদিনীপুর, জলেশ্বর, বালেশ্বর ইত্যাদি এলাকা নিয়ে ছিল সলিম খানের জমিদারী। এই এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিতে মুঘলদের দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করতে হয়।
সলিম খানের মৃত্যুর পর ভাইয়ের ছেলে বাহাদুর খান ক্ষমতায় আসেন। তিনিও একাধিকবার মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।
মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরের এলাকার নাম ছিল বাকলা চন্দ্রদ্বীপ, যা বর্তমানে বরিশাল নামে পরিচিত।
সেই অঞ্চলের শাসক ছিলেন পরমানন্দ রায়। নদীবেষ্টিত এলাকা হওয়ায় মুঘলদের ওই এলাকায় নিয়ন্ত্রণ করতে বেশ বেশ পেতে হয়েছিল।
মুঘলদের হাতে যেভাবে বারভূঁইয়াদের পতন
বহু বছর ধরে মুঘল সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে এলেও অবশেষে সেই বিদ্রোহে যবনিকা টেনে দেন মুঘল সেনাপতি ইসলাম খান।
রাজা মানসিংহের শরীর ভেঙ্গে পড়তে শুরু করলে তিনি অবসর নেন। ইতোমধ্যে দিল্লির শাসন ক্ষমতায় এসেছে পরিবর্তন। আকবরের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় এসেছেন সম্রাট জাহাঙ্গীর।
পরবর্তীতে বেশ কয়েকজনকে সুবাদার হিসাবে মুঘল সম্রাটেরা পাঠালেও তারা ভূঁইয়াদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। যদিও মুঘল বাহিনীরও পুরোপুরি সুবিধা করতে পারেনি।
এরপর ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন ইসলাম খান চিশতী। তার মূল লক্ষ্য ছিল বারভূঁইয়াদের পরাস্ত করা।
‘বাংলার ইতিহাস’ বইতে সুনীতিভূষণ কানুনগো লিখছেন, প্রথমে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণে আলাপসিং পরগণা দখল করে ওসমান খানকে বিতাড়িত করেন।
এরপর দক্ষিণ বাংলার শাসক সলিম খানকে পরাস্ত করেন। বর্তমান নড়াইলের কাছে ছিল ভূষণার অধিপতি সত্যজিৎ এর রাজত্ব। একটি মুঘল বাহিনী পাঠিয়ে তাকে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন।
সেসময় বিশাল মুঘল বাহিনী নিয়ে ঘোড়াঘাটে অবস্থান নিয়ে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য, কামতা (কুচবিহার) রাজার রক্ষীনারায়ণ এবং সুসাঙ্গের রাজা রঘুনাথকে পরাস্ত করেন।
এরপর বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে করতোয়া নদী বরাবর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন ইসলাম খান। শাহজাদপুরের ভূঁইয়া রাজা রায় তাকে বাধা দিলেও পরাজিত হন।
সুনীতিভূষণ কানুনগো লিখেছেন, “ইসলাম খানের আগমনের খবর পেয়ে ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁর নেতৃত্বে বাংলার ভূঁইয়ারা একত্রিত হন। তাদের মধ্যে ছিলেন ভাওয়ালের বাহাদুর গাজী ও তার পুত্র সোনা গাজী, বানিয়াচঙ্গের আনোয়ার গাজী, মির্জা মুমিন, খলসীর মধু রায়, চাঁদ প্রতাপের বিনোদ রায়, মাতঙ্গের পাহলোয়ান।
ইছামতী নদীর তীরে যাত্রাপুর নামক স্থানে তারা অবস্থান নিয়ে দুর্গ তৈরি করেছিলেন। সেটি দখল করে নেয় মুঘল বাহিনী। এরপর ডাকচরা দুর্গও দখল করে।
সুবাদার ইসলাম খান ঢাকায় প্রবেশ করে ঢাকাকে রাজধানী ঘোষণা করেন এবং সম্রাটের নামে তার নতুন নামকরণ করেন – জাহাঙ্গীরনগর।
এরপর সেখান থেকে বারভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে শুরু করেন।
মুসা খাঁর নেতৃত্বে ভূঁইয়ারা আবার সমবেত হচ্ছিলেন। তখন এগারসিন্দুর থেকে সোনারগাঁ পর্যন্ত বহু সামরিক ঘাটি তৈরি করেছিল ভূঁইয়া বাহিনী।
ইসলাম খানও সেজন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।

এরপর ১৭১১ সালে মুসা খাঁর সামরিক ঘাঁটি কাত্রাভু দুর্গের ওপর হামলা শুরু করে মুঘল বাহিনী। সেটা দখলে নেয়ার পর একের পর এক সামরিক ঘাঁটি দখল করতে করতে সোনারগাঁ এসে হাজির হয়। তুমুল লড়াইয়ের পর মুঘল বাহিনী সোনারগাঁ দখল করে নেয়।
সুনীতিভূষণ কানুনগো লিখেছেন, “সম্ভবত এটাই মুঘলদের বিরুদ্ধে বারভূঁইয়াদের সর্বশেষ সম্মিলিত সংঘর্ষ। …মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরবর্তী সমগ্র অঞ্চল মুঘল অধিকারভুক্ত হইল। প্রতিরোধকারী নেতারা অতঃপর মুঘল প্রশাসনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করিলে তাহাদের সামরিক ও প্রশাসনিক বিভাগে উচ্চপদ দেওয়া হইল।”
কিন্তু তখনো কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা মুঘলদের নিকট নতি স্বীকার করেননি।
যেমন রাজা প্রতাপাদিত্য আগে বশ্যতা স্বীকার করলেও, নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে শুরু করেন। বরং তিনি সেনাবাহিনী এবং নৌবাহিনী শক্তিশালী করতে শুরু করেন, এক পর্যায়ে যুদ্ধে পরাজিত অনেক পাঠান তার বাহিনীতে যোগ দিতে শুরু করে।
এই খবর পেয়ে ইসলাম খান মুঘল সেনাবাহিনী যশোরের দিকে পাঠান। তাতে নৌ ও স্থলযুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। তাকে বন্দি করে দিল্লি পাঠানো হলে পথে তার মৃত্যু হয়।
এরপর বাকলা বা বরিশালের দিকে মুঘল বাহিনী পাঠান ইসলাম খান। সেখানকার জমিদার রামচন্দ্র পরাজিত ও বন্দি হন। এর মাধ্যমে পুরো দক্ষিণ বঙ্গ মুঘলদের নিয়ন্ত্রণে আসে।
কিন্তু মুঘল বাহিনী সবচেয়ে বড় প্রতিরোধে মুখে পড়েছিল ভাটি অঞ্চলের ওসমান খানের সামনে।
বুকাইনগরে শাসন কেন্দ্র স্থাপন করে তিনি শক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তার সঙ্গে শ্রীহট্টের আনোয়ার খান, বায়েজিদ কররানীও যোগ দিয়েছিলেন।
এরপর ১৭১২ সালে দক্ষিণ শ্রীহট্টে মুঘল বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন ওসমান খান।
তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা অঞ্চলে মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে ভূঁইয়াদের প্রতিরোধ সংগ্রামও শেষ হয়ে যায়।
# সায়েদুল ইসলাম, বিবিসি নিউজ বাংলা